অনিন্দ্য পাল
"ডুগডুগি বাজালেই ছেলেরা সেখানে ছুটে যায় ... কেউ কেউ উলঙ্গ হয়ে চলে আসে। কোনও খেয়াল থাকে না। সেরকম আপনারাও তাদের টেনে আনুন - বিজ্ঞানের ডুগডুগি বাজিয়ে। যা শিখেছেন, বিজ্ঞানের যে খবরটি পড়েছেন সেগুলিকে তাদের কাছে নিয়ে যান ... এতে মানুষের কল্যাণ হবে, দেশের উন্নতি হবে। "--এই মন্তব্য যার, বাঙালি তাকে এখন ভুলতে বসেছে। তিনি বাঙালি বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য।
আত্মপ্রচারবিমুখ এই প্রকৃতি বিজ্ঞানী একদিকে যেমন আজীবন খুব কম আয়োজনে বিজ্ঞান গবেষণা করেছেন তেমনি বিজ্ঞানের কঠিন ও জটিল বিষয় গুলোকে সহজ সরল ভাবে সাধারণ মানুষের উপযুক্ত করে প্রকাশ করেছেন, যাকে বিজ্ঞান- সাহিত্য বলাই যায়।
গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের বিজ্ঞানী হয়ে ওঠা আসলে একটা সংগ্রামের ইতিহাস। প্রথাগত শিক্ষায় ম্যাট্রিক পাশ হলেও বিজ্ঞান চর্চার একটা নতুন দরজা খুলে দিয়েছিলেন। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে আইএ তে ভর্তি হলেও আইএ পাশ করা হয়ে ওঠেনি।
সংসার চালানোর জন্য স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে আবার জন্মভূমি ফরিদপুরের লোনসিং এ। প্রথমে পাশের গ্রামের পাতিসার হাইস্কুলে তারপর লোনসিং হাইস্কুলের ভূগোলের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এই লোনসিং-এ ১৮৯৫ সালের ১লা আগস্ট তিনি জন্মেছিলেন। গরীব ব্রাহ্মণ বাবা অম্বিকাচরণ যখন মারা গেলেন গোপালচন্দ্র তখন মাত্র পাঁচ বছরের ।
ফলে আর্থিক কষ্টের বেড়া ডিঙিয়ে এগোনোর এক চরম লড়াই তার ভবিতব্য হয়ে গেল। তবে এই কঠিন পরিস্থিতি তাকে দমিয়ে দিতে পারেনি। যার প্রতিফলন তার সমস্ত জীবন ধরে দেখা যায়। গাছপালা কীটপতঙ্গ ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। যেখানেই পোকামাকড় বা পতঙ্গ বিষয়ে কিছু নতুন দেখতেন সেখানেই একটা আতসকাচ নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিতেন। এই রকম গবেষণা করতে গিয়ে অনেক খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। যেমন একবার কোলকাতা ছাড়িয়ে সোনারপুর অঞ্চলে এই রকম পোকামাকড় খুঁজতে হাজির হন। একটা দীঘির আশপাশে ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে তিনি পিঁপড়ের মধ্যে লড়াই দেখতে পান। তক্ষুণি তিনি ছবি তুলতে লাগলেন আর ঘটনাটা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর এই কাজ দেখে কিছু ভিড় জমা হল। এই ভিড় কিন্তু তাকে অন্য কিছু ভেবেছিল। ফলে তারা গোপালচন্দ্র কে অনেক অপমান করতে লাগলো। কিন্তু গোপালচন্দ্র তাতে ভ্রূক্ষেপ না করায় সেই ভিড় তাঁকে রীতি মত ধাক্কাধাক্কি করে।এই রকম শারিরীক নির্যাতন তাকে শুধু যে এ সহ্য করতে হয়েছে তা কিন্তু নয়, আরও অনেক ক্ষেত্রেই এই রকম ঘটনা ঘটেছে। তবে এই সব অপমানজনক পরিস্থিতি তাঁর কাজ থামিয়ে দিতে পারেনি। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চালিয়ে গেছেন নিরলস গবেষণা। সঙ্গে লিখেছেন সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞান সাহিত্য।
তখন লোনসিং এ থাকেন। শিক্ষকতা করছেন লোনসিং হাইস্কুলে। একদিন জানতে পারলেন , গ্রামের পাঁচীর মার বাড়ি ভূতুড়ে আলো দেখা যাচ্ছে। মানুষ ভয়ও পাচ্ছে বিস্তর। গোপালচন্দ্র ঠিক করলেন এর রহস্য কি তা জানতে হবে। যেমন ভাবা, তেমন কাজ। একদিন রাতে চলে গেলেন পাঁচীর মার বাড়ি। যেমন টা তিনি ভেবে ছিলেন, এ কোন ভূত অদ্ভুত এর কাজ নয় -গাছপালা পচে যে গ্যাস বের হয় তার জন্যই জ্বলছে ওই আলো। অন্ধ-কুসংস্কার এর গোড়ায় দিলেন টান। গ্রামের মানুষ কে বুঝিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। "পচা গাছপালার আশ্চর্য আলো বিকিরণ করবার ক্ষমতা " নামে একটা লেখা পাঠালেন প্রবাসী পত্রিকায়। ১৯১৯ সালে প্রবাসীর পৌষ সংখ্যায় (১৩২৬ বঙ্গাব্দ) পঞ্চশস্য বিভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখার সূত্র ধরে গোপালচন্দ্র কে ডেকে পাঠালেন স্বয়ং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস এর মাধ্যমে। ১৯২১ সালে গোপালচন্দ্র যোগ দিলেন সদ্য প্রতিষ্ঠিত বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। তাঁর বিজ্ঞানী হবার পথে বলা যায় এটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।
গোপালচন্দ্র প্রধানত উদ্ভিদ আর পতঙ্গদের নিয়েই গবেষণা করেছেন। মানুষ ছাড়াও অন্য প্রাণীরাও যে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে যন্ত্র বা 'টুল' ব্যবহার করে সেটা তিনি "পিঁপড়ের বুদ্ধি " লেখাতে নিজের অভিজ্ঞতার সাহায্যে দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, 'কুমোরে পোকা ' নামে একটা পোকা কিভাবে ভারি মাটির টুকরো ব্যবহার করে গর্তের মুখ বন্ধ করে, কিভাবে ইয়ার উইগ পতঙ্গরা পিছনের পায়ে কাদা মাখিয়ে পা ভারি করে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে সেইসব ও খুবই সুন্দর ভাবে লিখে ছিলেন। তিনি ব্যঙাচির শরীরে পেনিসিলিন প্রয়োগ করে দেখিয়ে ছিলেন যে অ্যান্টিবায়োটিক কিভাবে ব্যঙাচির স্বাভাবিক বৃদ্ধি নষ্ট করে দিতে পারে।
গোপালচন্দ্রের আর একটা খুব বড়ো কাজ হল পিঁপড়েদের সমাজ জীবন, তাদের বাসা তৈরি আর যৌন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গবেষণাপত্র। তিনি নালসো পিঁপড়েদের দিয়ে সেলোফেন কাগজের মধ্যে বাসা বাঁধিয়ে ছিলেন। সেই স্বচ্ছ বাসায় পিঁপড়েরা কি করে, তাদের ঘর - সংসার, কর্মীদেরকে দিয়ে কাজ করানো এই সব ব্যাপারে যে গবেষণা করেছিলেন তা তখন খুবই বড় ব্যপার ছিল।
তাঁর গবেষণা থেকে স্ত্রী আর পুরুষ মাকড়সার সম্পর্কে অনেক অজানা খবর আমরা জানতে পেরেছি। পুরুষ মাকড়সাকে যে স্ত্রী মাকড়সা খেয়ে ফেলে, স্ত্রী মাকড়সা যে তার ডিমের ভয়ানক রকম যত্ন করে, এসব তিনিই জানিয়েছেন ।
তিনি বেশ কয়েক রকমের নতুন ধরনের মাকড়সা খুঁজে পেয়েছিলেন।
১৩২৫ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী'র পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় "রাঁড়া পেঁপে গাছের ফল" নামে একটা লেখা। যেখানে তিনি বলেন পেঁপে গাছে স্ত্রী এবং পুরুষ দু'রকম ফুলই ফোটে, তবে এরা আলাদা গাছে ফোটে।
স্ত্রী ফুলের গাছে ফল হয় কিন্তু পুরুষ ফুল গাছে ফল হয় না।
বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তিনি ১৬ টা গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। এগুলো ভারত এবং ভারতের বাইরের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তবে তাঁর গবেষণার খুব সামান্যই প্রকাশ হয়েছিল। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কিছু গবেষণাপত্র প্রকাশ পেলেও সেগুলো বিজ্ঞানীদের নজরে পড়েনি।
গোপালচন্দ্র আঘাতও কম পাননি। কলেজের, বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু উঁচু ডিগ্রী না থাকায় তাঁকে সমসাময়িক অনেক বিজ্ঞানীরাই স্বীকৃতি দিতে চাননি। এমনকি ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মাসিক "জ্ঞান ও বিজ্ঞান " পত্রিকার সম্পাদকের পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেবার নোংরা চেষ্টাও হয়েছিল। যদিও তাঁর মেধা আর লড়াকু চরিত্রের কাছে যাবতীয় চক্রান্ত হার মেনেছে। প্রথম দু'বছর সহযোগী সম্পাদক হিসেবে আর তারপর সম্পাদক, প্রধান সম্পাদক হিসেবে "জ্ঞান ও বিজ্ঞান " পত্রিকার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। জীবনের শেষ দিকে ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা।
বঞ্চিতও কম হননি। ১৯৫১ সালে প্যারিস থেকে ডাক পেলেন। সেখানে সামাজিক পতঙ্গদের উপরে আলোচনার নিমন্ত্রণ। কিন্তু যাওয়া হয় নি তার। আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিজ্ঞানীকে ডিএসসি সম্মান দিল যখন তিনি জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে। ১৯৮১ সালের ২১শে জানুয়ারি তিনি ডিএসসি পেলেন আর এর মাস দুই পর ৮ এপ্রিল তিনি মারা যান।
তবে সম্মান, ভালোবাসা কম পাননি। ১৯৬৮ সালে পেলেন আনন্দ পুরষ্কার। এই সম্মান ছিল তাঁর সাহিত্যের স্বীকৃতি। আবার ১৯৭৫ সালে 'বাংলার কীটপতঙ্গ ' বইটার জন্য পেলেন রবীন্দ্রপুরষ্কার। সহজ সরল ভাবে সাধারণ মানুষের উপযুক্ত করে বিজ্ঞান লেখায় তিনি বাকি সবাই কে পিছনে ফেলে দিয়েছিলেন। ভালোবাসাও পেয়েছিলেন সেই কাজের জন্য। অন্নদাশংকর রায়ের কথায় " পপুলার সায়েন্স তাঁর মত লেখবার ক্ষমতা খুব কম লেখকেরই আছে। এর কারণ পরের লেখা বই থেকে উপাদান সংগ্রহ করার চেয়ে স্বয়ং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাই তাঁর স্বভাব। তিনি একজন সার্থক গবেষক। সেইসঙ্গে একজন সার্থক লেখক। "
=====================
অনিন্দ্য পাল
গ্রাম -- জাফরপুর
পোঃ-- চম্পাহাটিি
পিন - ৭৪৩৩৩০
থানা -- সোনারপুর
জেলা -- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

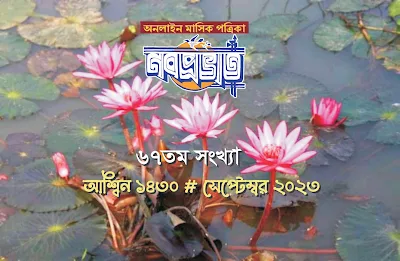










No comments:
Post a Comment